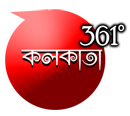তামিল গেরিলাদের হামলা থেমে গিয়েছে, এলটিটিই বিদ্রোহীদেরও দমন করা গিয়েছে, এমনকি তামিল বিদ্রোহীদের দমন করতে সরকারের খরচও ছিলনা। শ্রীলংকা সরকার যখন তামিল বিদ্রোহ থামাতেই সবথেকে বেশি ব্যস্ত তখনো ভাবা যায়নি দেশটা ১৭ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতিতে পড়বে, খাদ্যের অভাবে দিশেহারা হতে হবে মানুষকে, বিদ্যুতের অভাবে বন্ধ হবে কারখানার মেশিন, গ্যাসের বদলে লাকড়ি ব্যবহার করতে হবে, হাসপাতালে অসুস্থদের জন্য থাকবে না ওষুধ। শ্রীলঙ্কার মানুষকে যে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদেরই যুদ্ধ করতে হবে এমনটা ভাবতে পারেনি। তামিল বিদ্রোহ দমন করতে পেরেই শ্রীলঙ্কার সরকার যেমন নিজের ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদনের জন্য বেপরোয়া উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়েছিল তেমনি উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এসেছিল প্রশান্তির ভাব। রাজনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মতে শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই।
অর্থনীতির নিয়মানুসারে যে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি যত বেশি, যে দেশের আমদানিনির্ভরতা আর রফতানি মাত্রার মধ্যে ফারাক যখন বিরাট আকার ধারণ করতে থাকে তখন সে দেশ অর্থনীতিতে তত বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। শ্রীলংকার অর্থনীতিতে প্রথম আঘাত আসে যখন সে দেশের কৃষি বিদেশী মুনাফা চক্রের হাতে চলে যায়। এর পরে সে দেশের সরকার উন্নয়নের নামে হাতে নেয় বেশ কয়েকটি মেগা হাইব্রিড প্রকল্প। বস্তুতপক্ষে প্রকল্পগুলি ছিল নিম্নবিত্ত সাধারণ জনগণকে নিগৃহীত করে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তকে আকৃষ্ট করা। আমদানিনির্ভর অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত কিছু সুবিধা ভোগ করলেও নিম্নবিত্তের হাল হয় শোচনীয়। তাছাড়া কৃষি আর শিল্পকে যখন অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে তখন বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ে পড়ে ভাটা। তার সঙ্গে ঋণের বোঝা যখন জমতে জমতে পাহাড় হয়ে ওঠে তখন ‘উন্নয়ন’ প্রকল্প থেকে কিভাবে অর্থ উদ্ধার করা যায় সেই যজ্ঞে ঝাপাতে হয়।

শ্রীলঙ্কা সরকার তাই চীনের থেকে ঋণ নিয়ে বন্দর গড়ে চীনের কাছে লিজ দিতে বাধ্য হয়েছে। পরিবারকেন্দ্রিক রাজাপাকসের সরকারি নীতি যে শ্রীলংকার এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীলঙ্কা সরকারের এ ধরণের নীতির প্রধান আস্থাভাজন হল দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শ্রেণী। তার মানে সে দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ও রক্ত-মাংসে দুর্নীতিপ্রবণ। কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা অনুযায়ী যে ভোগ সংস্কৃতির উত্থান তা উচ্চাভিলাষী সরকারের জন্য আরামদায়ক। আমদানিনির্ভর অর্থনীতি আর দুর্নীতিনির্ভর ভোগবাদী সংস্কৃতি শ্রীলংকার আজকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী। সেই কারণেই সে দেশের আমলাতন্ত্র একের পর এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প সরকারকে উপহার দিয়েছে। উচ্চাভিলাষী আমলারা বড় বড় অংকের বিদেশী ঋণের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারা ভোগই প্রধাণ্য দেন, পরিণতির বিষয়ে থাকেন উদাসীন। উচ্চশিক্ষিত আমলারা তাদের ব্যাংক ব্যালান্সকে সিকিউরিটি মনে করেন। আর সরকার নিজের সিকিউরিটির জন্য আমলা ও বিদেশী শক্তির উপর আস্থা রাখেন।

একটি দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত, অথচ সে দেশের উচ্চশিক্ষিতরা দুর্নীতিগ্রস্ত পাশাপাশি সে দেশের সরকারের চরিত্রও একই রকম, তবে তো সে দেশের জনগণের ন্যুনতম অধিকার পদদলিত হতে বাধ্য। তবে সেই অবস্থার জন্য সে দেশের সুশীল সমাজও কি সমান দায়ী নয়? কারণ সুশীল সমাজের নিষ্ক্রিয়তা বা দুর্বলতার একটা বড় ভূমিকা থেকেই যায়, সেদিক থেকে তাদের দায় অনেক বেশি। একটা দেশে যখন যথার্থ কারণেও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সুশীল সমাজ গড়ে না ওঠে তখনই সরকারি নীতিগুলি হয় একপেশে, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন বাড়ে। শ্রীলংকার সরকার উচ্চশিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে সব ধরণের প্রচারমাধ্যমগুলিকে তাদের হাতের মুঠোয় রেখেছিল। তার পাশে সবাধীন ও স্বতন্ত্র শিক্ষিত সমাজ কোনওদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষিত সমাজে কোনও স্বকীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেনি, ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষিতরাই সরকারের পক্ষ নিয়ে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাজ করে গিয়েছে।

শ্রীলংকায় যে সত্যি কোনও সুশীল সমাজ বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নেই সেটা আরও স্পষ্ট হলো সরকার এতগুলি মেগা প্রজেক্ট নিয়ে চালালো। যাতে দেশের কৃষি দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হল, কৃষকদের জীবন বিপন্ন হল, আর দেশ ভরে গেল প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে। ২০১৯ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘শ্রীলঙ্কা ইজ এ ক্ল্যাসিক টুইন ডেফিসিট ইকোনমি’। অর্থাৎ একটি দেশের জাতীয় আয়ের চেয়ে জাতীয় ব্যয় বেশি এবং দেশটির বাণিজ্যিক পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন যথেষ্ট কম। বিশ্লেষকদের বক্তব্য, শ্রীলঙ্কা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বন্ড বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে নির্বিচারে বিক্রি করেছে। সামনে পিছনে কোনও চিন্তা না করে ডলারে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করা ঋণখেলাপি শ্রীলঙ্কার সর্বনাশের মূল কারণ। ডলারভিত্তিক ওই সঞ্চয়পত্র দেশটির সর্বমোট বৈদেশিক ঋণের প্রায় অর্ধেক। শ্রীলঙ্কা সরকার সঞ্চয়পত্রের কিস্তিভিত্তিক মুনাফার অর্থ দিতে দিতে না পারায় রাষ্ট্রীয় সঞ্চয়ে ডলারের পরিমাণ শূন্যে এসে ঠেকেছে।
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল সরকারের এই দুর্নীতিগ্রস্ত নীতি একনাগাড়ে চলতে থাকলেও শিক্ষিত বা সুশীল সমাজ থেকে কোনও জোরদার আওয়াজ ওঠেনি। সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির ভবিষ্যৎ কি হতে পারে তার কথা ভেবেও কোনও প্রতিবাদ কোনও আন্দোলন দানা বাঁধেনি। ছাত্রসমাজ থেকেও আওয়াজ উঠতে পারতো, তারাও সেই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। এখন যে আগুন জবলছে তা সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিলেও সেখানে কি সঠিক কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য বা দিশা আছে? ‘শুট অ্যাট সাইট’ নির্দেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের মনোভাব অনেকটা যেন ‘সিংক অর সুইম’। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির একটা সংকট রয়েই গিয়েছে।